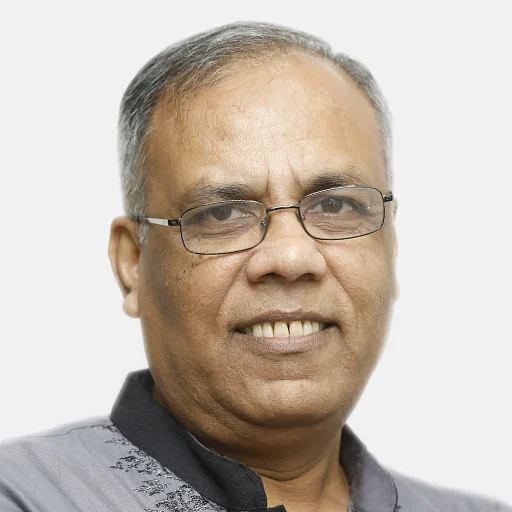শত্রুর (বিএনপি, গণতন্ত্র মঞ্চ, সিপিবি অথবা সরকারবিরোধী যেকোনো দলের নাম পড়া যেতে পারে) মুখে ছাই দিয়ে আগামী ৭ জানুয়ারির নির্বাচন নামক আয়োজন প্রমাণ করে দিচ্ছে, দেশে আসলেই চমক লাগানো উন্নয়ন হয়েছে। নির্বাচনের জন্য যে হলফনামা দিতে হয়, সম্পদের বিবরণ ও আয়কর দেওয়ার প্রমাণ দিতে হয়, তা থেকে প্রার্থীদের সম্পদ ও আয় বৃদ্ধির যেসব চিত্র পাওয়া গেছে, তাতে যাঁরা উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন করেন, তাঁদের নিশ্চয়ই মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা।
মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় বৃদ্ধির হিসাব নিয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারে না। সপ্তাহ দুয়েক ধরে সংবাদমাধ্যমে প্রার্থীদের সম্পদ ও আয় দুটোই কমেছে, এমন কারও কথা শোনা গেল না।
৯০ শতাংশের সম্পদ বেড়েছে; কারও ৪ গুণ, কারও ৪০ গুণ, সর্বোচ্চ ৬০ গুণের বেশি। বর্তমান যুগে কারও কাছে নগদ টাকা কোটির বেশি থাকতে পারে, এমনটা ধারণা করাও কঠিন। কিন্তু আছে; কারও কারও কাছে কয়েক কোটি নগদ টাকা আছে।
তবে সরকারবিরোধীরা নির্বাচন না করায় নির্বাচন শুধু যে একতরফা হচ্ছে তা–ই নয়; সরকার–সমর্থকদের সমৃদ্ধির চিত্র প্রকাশের ব্যাপারটাও একতরফা হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে ‘ব্যাংক ডাকাত’, ‘শেয়ারবাজার লুটেরা’, ‘দুর্নীতির রেকর্ডধারী’, ‘টাকা পাচারকারীর’ মতো নানা ধরনের বিশেষণ একটু বেশিই শোনা যাচ্ছে। এখন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বলছে, ১৮ জন শতকোটিপতি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। আর প্রার্থীদের ৮৭ শতাংশই কোটিপতি।
আওয়ামী লীগের উন্নয়নের ধারা শুরুর আগে কোটিপতি প্রার্থী ছিলেন ২৭ শতাংশ। তারা একজন মন্ত্রীর বিদেশেও হাজার আড়াই কোটি টাকার সম্পদের তথ্য তুলে ধরে বলেছে, তিনি হলফনামায় এসব তথ্য দেননি। অতএব অনুমান করা অন্যায় হবে না যে হলফনামায় সবাই সব সম্পদের হিসাব দেননি। এসব হিসাব আবার সম্পদ কেনা হয়েছে যে দামে, সেই হিসাবে, বর্তমান বাজারমূল্যে নয়। বর্তমান বাজারমূল্যে হিসাব করলে তা বহুগুণে বেড়ে যাবে।
ক্ষমতায় থাকার বা ক্ষমতাসীনদের পক্ষে থাকার এত যে আর্থিক সুবিধা, সেটা নিয়ে অনেক কানাঘুষা ছিল। কিন্তু এখন আমরা তা নিশ্চিত তথ্য হিসাবে জানতে পারছি।
রাজনীতির আসল প্রতিদ্বন্দ্বীদের বাদ দিয়ে নকল প্রতিদ্বন্দ্বী (ডামি প্রার্থী) দাঁড় করিয়ে যে নির্বাচন সাজানো হয়েছে, তাতে ভোটাররা পছন্দের প্রতিনিধি বেছে নেওয়ার সুযোগ না পেলেও এ আয়োজন থেকে অনেক কিছুই জানতে পারছেন। আমরাও রাজনীতির নতুন নতুন কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা নিচ্ছি।
উন্নয়নবিষয়ক জ্ঞানলাভ ছাড়া এ পর্যন্ত আর কী কী শিক্ষা পাওয়া গেল, তার একটা তালিকা দাঁড় করানোই আজ আমার অনুশীলন। যা কিছু বাদ পড়ে যাচ্ছে, তার জন্য অধমের অজ্ঞতাকে ক্ষমা করে দিয়ে নিজেরা প্রয়োজনমতো তালিকাটি সমৃদ্ধ করতে পারেন।
* বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ের চেয়ে অন্তর্দলীয়, গোষ্ঠীগত বা উপদলীয় লড়াই গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করে। যে কারণে দলীয় টিকিটে ২৬৩ জনকে মনোনয়ন দিলেও দলের ২৬৯ জনকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার অনুমতি দেওয়া সম্ভব।
* দলের গঠনতন্ত্রে দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হওয়া সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়ার কথা থাকলেও এবং অতীতে এ অপরাধে শত শত দলীয় নেতা–কর্মীকে বহিষ্কার করা হলেও গণতন্ত্রকে নতুন রূপ দেওয়ার জন্য তা সহি।
* বিরোধী দল নির্বাচনে থাকলে পাল্টাপাল্টি প্রচারযুদ্ধ যতটা হিংস্র বা সহিংস হওয়ার আশঙ্কা করা হয়, দল ও জোটের আসল ও নকল প্রার্থীর প্রচারযুদ্ধ তার চেয়ে বেশি উগ্র ও রক্তক্ষয়ী হওয়া কোনো সমস্যা নয়। এ রকম লড়াইয়ে তিনজনের প্রাণহানির পরও পরিস্থিতি নিয়ে ন্যূনতম উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং বাংলাদেশে নির্বাচনের সঙ্গে মারামারি ও রক্তারক্তি যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রমাণ, তা তুলে ধরাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।
* উপদলীয় ও গোষ্ঠীগত সংঘাত ইতিমধ্যেই যতটা ব্যাপকতা পেয়েছে, তাতে বিরোধীদের আন্দোলনের কথিত নাশকতা জনমানসে অচিরেই হারিয়ে যাবে।
* নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়াতে শুধু দল নয়, মহাজোটেও গোষ্ঠীগত লড়াইকে উৎসাহিত করা। এর ফলে ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ, জাতীয় পার্টির নেতারা নামকাওয়াস্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাইলেও এখন আসন হারানোর আশঙ্কায় নিদ্রাহীন রাত কাটাচ্ছেন। আগে তাঁরা যতগুলো আসনে ছাড় পেয়েছিলেন, এবার তা অর্ধেকে নামায় তাঁরা বুঝতে পারছেন, ভবিষ্যতে বড় নেতাদের টেবিলে তাঁদের জন্য আর কোনো জায়গা থাকবে না।
* বিরোধী দলকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখার পর রাজনীতি থেকে নির্বাসিত করার লক্ষ্য অর্জনে এমন ব্যবস্থা নেওয়া, যাতে অনুগতদের মধ্য থেকেই নকল (ডামি) বিরোধী দল দাঁড় করানো সহজ হয়। তবে তারা যাতে কোনোভাবেই আত্মনির্ভর হতে না পারে, সে জন্য আসন ভাগাভাগিতে বিরোধী দলের মর্যাদার জন্য প্রয়োজনীয় ৩০ আসনের চেয়েও কম – ২৬ আসনে ছাড় দেওয়া।
* গণতন্ত্রের এই নতুন ধারায় দলবদলে রাজি হলেই, অর্থাৎ বিএনপির সঙ্গ ছাড়লেই জামিনে মুক্তি ও নৌকার মনোনয়ন—দুটোই যে মেলে, শাহজাহান ওমর তার প্রমাণ রেখেছেন। বিরোধী নেতার ওজন বুঝে নৌকার প্রার্থীকে সরিয়ে নেওয়াও যে অসম্ভব নয়, তারও প্রমাণ রেখেছেন জেনারেল সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম।
* নির্বাচনে দলের অংশগ্রহণ প্রতিনিধিত্বমূলক না হলে বা প্রশ্নবিদ্ধ হলে ধরেবেঁধে এনে হলেও ভোটার উপস্থিতি বাড়ানোর কর্মসূচি গ্রহণ। এ ক্ষেত্রে বৈধ, অবৈধ বা নীতিনৈতিকতার কোনো বালাই নেই। রাষ্ট্রের হাতে যত রকম হাতিয়ার আছে, তার সবই প্রয়োগ করা যায়। প্রান্তিক ও বিপন্ন মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে হলেও ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে হাজির করার নতুন নজির তৈরি করা। সন্দেহ নেই, গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ভাতার বড় ধরনের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে, যার সংখ্যা সরকারি হিসাবে এখন ১ কোটি ২৮ লাখ। সংখ্যাটা মোট ভোটারের প্রায় ১১ শতাংশ। দুর্দিনের বাজারে মাসিক ভাতা হারানোর ভয় তো উপেক্ষা করার মতো কিছু নয়।
* স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা এবং সিটি কাউন্সিল কর্মকর্তারা নাগরিকদের যেসব সেবা দেওয়ার জন্য আইনগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাঁরা যেহেতু প্রায় সবাই ক্ষমতাসীন দলের (বিএনপির অতীত বর্জনের কারণে) সদস্য। তাঁদের কেউ কেউ হুমকি দিয়েছেন, ভোটকেন্দ্রে যাঁরা যাবেন না, তাঁরা তাঁরা কোনো সেবা পাবেন না।
* ২০১৮ সালের নির্বাচন যাদের কল্যাণে রাতের ভোট হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে, তাদের একাংশ পুলিশ এখন অতি উৎসাহী হয়ে ভোটার হাজির করার অভিযানে নেমেছে। ঢাকায় তারা সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলরদের ভোটার হাজির করার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। পুলিশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বের কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু তাদের ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে নেওয়ার দায়িত্ব বা কর্তৃত্ব কোন আইনে আছে? দেশের বিরোধী দলগুলো যখন ভোট বর্জনের আহ্বান জানাচ্ছে, তখন তাদের উদ্যোগকে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি বিশেষ সেবার নতুন নজির ছাড়া আর কিছু কি বলা চলে?
দেশে ভোট দেওয়া আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক নয়, আবার কাউকেই পছন্দ নয় জানানোর এমন ব্যবস্থা ব্যালটে নেই। এমনকি, নষ্ট ব্যালটের সংখ্যা মোট ভোটের অর্ধেকের বেশি হলেও নির্বাচনের ফল বা বিজয়ী ঘোষণায় কোনো বাধা নেই। এর ফলে কোনো পছন্দ না থাকলেও ভোট দিতে বাধ্য করা অত্যাচারের সঙ্গেই তুলনীয়।
নাগরিকদের ন্যায্য প্রাপ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সুবিধাকে দলীয় লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার করার যেসব নীতিহীন পদক্ষেপ এবং ভয় দেখানোর মাধ্যমে জবরদস্তি করে ভোট আদায়ের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হচ্ছে, ভবিষ্যতে তার শিকার যে আওয়ামী লীগও হতে পারে, সে কথা তারা হয়তো বিস্মৃত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস বলে, ১৯৭৪ সালে তাদের তৈরি বিশেষ ক্ষমতা আইনে আশির দশকে তারাই সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার হয়েছিল।
* কামাল আহমেদ সাংবাদিক-কলামিস্ট, সাবেক সম্পাদক বিবিসি বাংলা ও প্রথম আলোর সাবেক কনসাল্টিং এডিটর