ঘুম থেকে যখন জাগলাম দেখি ভিন্ন ঘর অন্য ছবি। হা করে আছে জানালা-কপাট। সেই পথে ঢুকছে বাতাস বাধাহীন। আম্মা গোছগাছ করছেন ছড়ানো ছিটানো জিনিসপত্র। আব্বা আর বড়মামা দূরে বারান্দায়। আমার অবাক চোখ। বাইরে যাচ্ছে বারবার ফিরে আসছে একঝুড়ি জিজ্ঞাসা নিয়ে। অপরিচিত দৃশ্য, অচেনা মানুষ। এরিমধ্যে হাঁটতে শিখে ফেলেছি। উঠানে যেতে চাইলাম, আম্মা আটকে দিলেন। দরজার ধারেকাছে ভিড় করেছে বেশ ক’জন ছেলেমেয়ে। আমার সমবয়সি এরা। বড়ও হবে হয়তো দু’একজন। খেলতে ইচ্ছে করছে ওদের সাথে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। আম্মার উপর রাগ হচ্ছিল ভীষণ। অবশেষে উপায় ধরা দিলো। ঘরের দাওয়ায় পা রাখলাম। আমার মুঠোতে আম্মার আঙ্গুল। সামনে বাঁয়ে ডানে সবদিকে আটকে যাচ্ছে নজর। আকাশের আয়তনও ছোট ছোট লাগছে। এখানকার আকাশ এতো ছোট কেনো। আম্মাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে। বাতাসে উড়ে না ধান পাতার গন্ধ। দূর্বাঘাস তারও দেখা নেই। পরিচিত বন্ধুরা যে কোথায় গেল কে জানে। পরিবেশে অদল-বদলের হাওয়া।
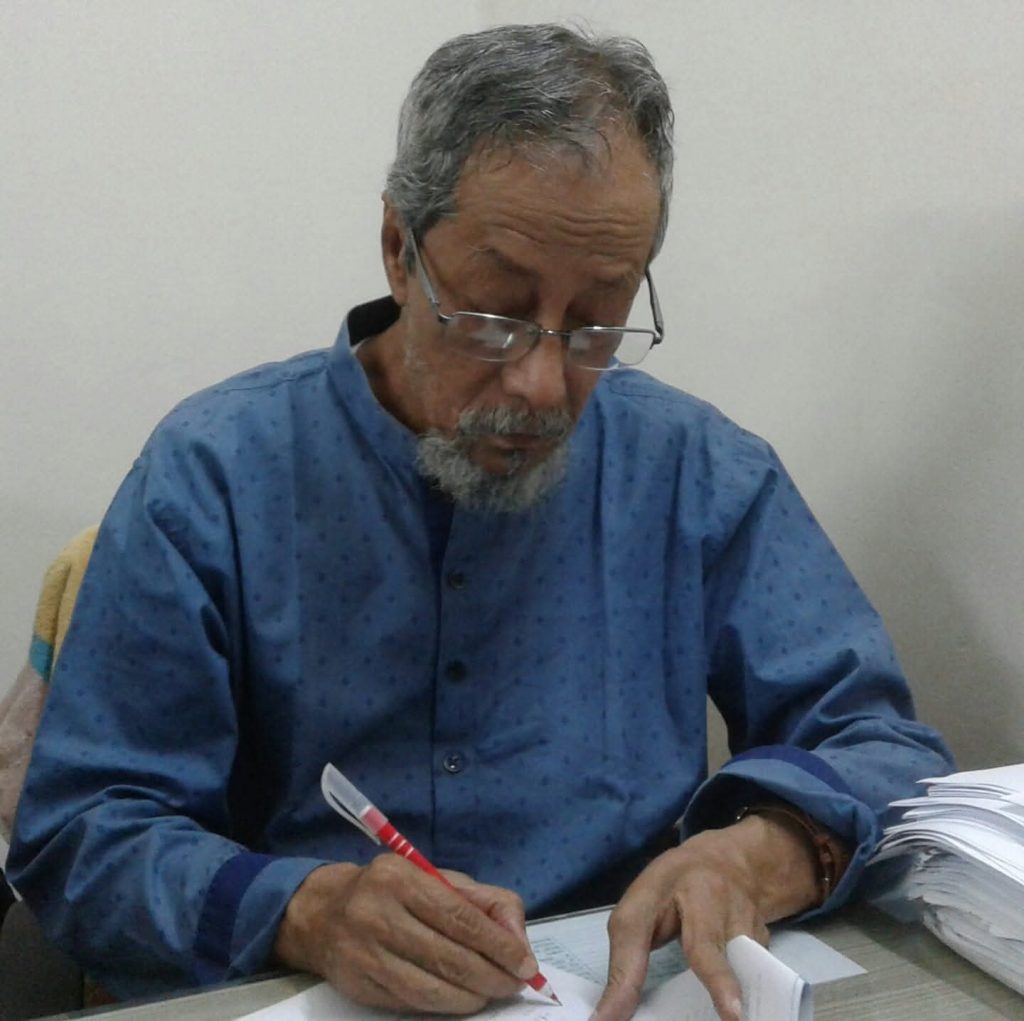
ছড়ানো ছিটানো ঘর-বাড়ি। তেল চিটচিটে দালানকোঠাও দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। কোনোটার আস্তর খসে পড়েছে। কোনোটা আবার হা করে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। এসব দালানের অনেকগুলোরই ভাঙ্গা বুক, ভাঙ্গা মাথা। আমরা যে দালানটিতে উঠেছি সেটিরও বয়স হয়েছে। ছালবাকল উঠে গেছে। বেড়িয়ে পড়েছে লাল হাড়গোড়। চোখের দৃষ্টিতে ছানি। তারপরও দালান বলে কথা। মেজাজই অন্যরকম। কোথাও কোথাও আবার গা ঘেষাঁঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সব একতলা এর বেশি। কচিৎ নজরে আসে। পাশাপাশি ক’জন পরিবারের বসবাস কে জানে। তখনো আমি গুনতে শিখিনি। এক দুই তিন এর নামতা কানে আসে। আশপাশের বাড়ি-ঘরে কারা যেন পাঠ করে রোজ! সকালে আর সন্ধ্যায় এমন আওয়াজ উড়তে থাকে। তারপর জানালা গলিয়ে পৌঁছে যায় আমার কানে। তাই উড়ে আসা শব্দগুলো বন্ধু হয়ে যায় এক সময়। বন্ধুদের সাথে কথা হয়, দেখা হয়। কিন্তু পরিচয় হয় না। কেবল চোখ চাওয়া চাওয়ি। আম্মা একদিন ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আঙ্গুল টিপে টিপে। এক দুই তিন চার পাঁচ। এই পাঁচ পর্যন্ত গিয়েই দাঁড়িয়ে থাকলাম। দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই। তবে বেশি দিন দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি। হাঁটতে শুরু করলাম টুকটাক। দু’হাতের দশ আঙ্গুলকে ধারাপাত বানিয়ে দিলেন আম্মা, এক সময়। মনে হলো আনন্দের দিঘিতে সাঁতার কাটছি। তখন আড়াই-তিন বছরের বেশি হবে না বয়স, হয়তো। বুঝ-বিবেচনার কলি ফুটবে ফুটবে ভাব। এই যখন সময় তখন কলির উপর শিশির ঝরে, ঝরে রোদের কণা। চুমকুরি দেয় বাতাস। বাতাসের কোলে দোল খায় সময়। দোল খেতে খেতে পুষ্ট হয় পাপড়ি ডগা। জমা হয় গন্ধ সুবাস। এরিমধ্যে দু’একটি শব্দও ঠোটের ফাঁক গলিয়ে বাইরে আসতে শুরু করেছে। পাপড়ি আর সুবাস একাকার তখন। ফুলে-পাতায় লাফিয়ে পড়ে হাওয়া। গন্ধে মাখামাখি করে বয়সের সিঁড়িতে পা রাখছি।
বাইরে যেতে মানা। তাই জানালার শিক ধরে দঁাঁড়িয়ে থাকি সকাল-দুপুর। দৃষ্টি আকাশ ফুটু করে উঠতে চায় আরো উপরে। কিন্তু পারে না। ফিরে আসে দ্রæত। ঝিমধরা আকাশে একটি কি দু’টি পাখি উড়েতো। পাখা টান টান করে ভাসতো হওয়ায়, উলটি পালটি দিতো। তখন আনন্দের বাগানে ঢুকে পড়তাম। আম্মার রান্নাবান্নার সময় ছিল সেটি। মাঝেমধ্যে খোঁজ নিতে আসতেন। আমার দৃষ্টি তখনো পাখির ডানায় ঝুলে থাকে। এই ঝুলাঝুলি চলতো দুপুর অবধি। দুপুর নামতে শুরু করে নিচে, পশ্চিমে, আব্বা তখন ঘরে ফিরতেন। এমনটা ছিল প্রায় প্রতিদিনের রোজনামচা। বাইরে যাওয়া আর ঘওে ঢোকার ফর্দ। কোথায় যান, কেন যান এমন ভাবনা হাঁটাহাঁটি করতো মাথায়। এই হাঁটাহাঁটিই সার। পথ হারাতো মাঝপথেই। এত ছোট্ট মগজে হাত পা ছুড়াছুড়ি করার সুযোগই বা কতটুকু। ভাষা ভাবনা ঝিম মেরে বসে থাকে। দূরে দাঁড়িয়ে আছে নিমগাছ, বেশ বড়সর। বাতাস আর নিমপাতার ঝিরঝির শব্দ ভাসতো শূন্যে। ওদের ফিসফাস আর কানাকানি অন্যরকম পরিবেশে দাঁড় করিয়ে রাখে আমাকে। একটি দু’টি দৃশ্য আটকে আছে মগজে, চোখের তারায় এখনো। ফ্রেমে বাঁধাই করা ছবির মতো, ঘরের দেয়ালে লটকে থাকে যেমন। রোজ আসতো লোকটি, কোমরের কাছে ঝুলতো বড়সর একটি চামড়ার ব্যাগ। সে ব্যাগ চুঁইয়ে ঝরতো দু’এক ফোঁটা পানি, টুপটাপ। লোকটি এলেই কলসি এগিয়ে দিতেন আম্মা। কখনো মোহাম্মদ আলী ভাই। তখন সেই চামড়ার ব্যাগের পেট থেকে বেড়িয়ে আসতো পানি, লাফিয়ে পড়তো কলসিতে। আশপাশের বাড়ি-ঘরগুলোর দরজায়ও জমতো ভিড়। ব্যাগওয়ালা কখন আসবে সে আশায়। পরে জেনেছি এমনি চামড়ার থলিতে যারা পানি ফেরি করে ওদের নাম নাকি ভিসতিওয়ালা। এসব ভিসতিওয়ালারা দূর থেকে পানি জোগাড় করে আনতো। বাড়ি বাড়ি ফেরি করতো পয়সার বিনিময়ে। পানির ঠিকানা কোথায় ছিল তখন জানতাম না। ধারেকাছে কোথাও ছিল হয়তো। ভিসতিওয়ালারা যে পানি বাসায় পৌঁছে দিত তা ছিল খাবার পানি। সব বাড়ির আম্মারা সে পানি যতœ করে সামলে রাখতেন। কারণ তখনকার দিনে বাসায় বাসায় টিপকলের ব্যবস্থা ছিল না। দু’তিন বাড়ি মিলেঝিলে ছিল কূপ। গোসল- ধোয়ামুছা সারতে হতো কূয়াতলায়। আর ভিসতিওয়ালারা ছিল পিপাসা মিটানোর ভরসা। একটা আলাদা মায়া জমে গিয়েছিল ভিসতিওয়ালার প্রতি। তাই রোজ অপেক্ষা করতাম, পথের ফাঁকফোকরে তাকাতাম বারবার। কখন আসবে সেই স্বপ্নের মানুষটি। ভিসতিওয়ালার থলে থেকে পানি বেড়িয়ে আসার দৃশ্য চমৎকার লাগতো। পানির শেষ ফোঁটাটি ঝরা পর্যন্ত চোখ সেখানে আটকে রাখতাম। মাঝে মাঝে আমার থুতনিতে আঙ্গুলের টোকা দিত, চামড়ার থলেটি ভাঁজ করতে করতে পানি বেগওয়ালা। আমিও চোখ লাগিয়ে রাখতাম এই আজব লোকটির চলে যাবার পথে, যতক্ষণ না মিলিয়ে যায়। কোথায় গেল পানি ফেরিওয়ালা? এমন ভাবনা ঘুরতো ফিরতো মনে। তারপর একসময় ছিঁড়ে যেতো চিন্তার সূতাগুলো।

দুই.
আব্বার কোলে উঠে বাড়ির বাইরে গেলাম একদিন। এই প্রথম শহর দেখা। এই শহরের যে কি নাম কেউ বলেনি আমাকে। বয়সের কলি যখন মেলি মেলি ভাব, তখন কে যেন বলেছিল এর নাম ঢাকা শহর। দূরে দূরে ঘর-বাড়ি। ঝোপঝাড় গাছপালা, এর ফাঁকফোকরে একটি দু’টি ঘর। এক দু’জন মানুষ হাঁটাচলা করে। কোনো কোনো বাড়ির উঠানের ধার ঘেঁষে ফুলগাছ। আরো কি কি গাছ যেন সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। ফুলের পাপড়ি, গাছের পাতা ছুঁতে ইচ্ছে করতো। আব্বার কোলে বসে এদিক সেদিক নজর ফেলতাম। ছোট্ট চোখে আর কতটাই বা শক্তি রাখে। কিছুদূর গিয়েই হোঁচট খেতো, ফিরে আসতো আবার নিজের কাছে। আব্বা হাঁটলেন কতকটা সময় আমাকে নিয়ে, প্রায় সুনসান পথে। আগে বাড়তেই আর একটি পথ। এ বয়সেও বুঝতে অসুবিধা হয়নি এপথ অন্যরকম। বেশ বড়সর। কোথায় যেন যাচ্ছে মানুষজন। দু’টি পশু দৌড়াচ্ছে। পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে চাকাওয়ালা বিশাল একটি কাঠের বাক্স। শব্দ হচ্ছে ঠকঠক। আমার চোখ দু’টি বড় হয়ে গেল, এমন অবাক বাক্স দেখে। বাক্স আবার কি করে হাঁটে, দৌড়ায়। কচি মগজে খোঁচা লাগে ভাবতে গিয়ে। আরো দু-তিনটি বাক্স দৌড়ে গেল। এরকম দৃশ্য আমার অবুঝ মনকে সবুজ বাগানে পৌঁছে দিয়েছিল। আব্বার মনেও তখন আনন্দ ছলাৎ ছলাৎ। দৌড়ে যাওয়া পশু এবং বাক্সগুলো দেখিয়ে তিনি কি যেন বুঝাতে চাইলেন আমাকে। হয়তো বলেছিলেন ঐ যে দৌড়ে যাচ্ছে বাক্সগুলো সেগুলোকে বলে ঘোড়ার গাড়ি। ঘরে ফিরে আম্মাকে বলেছিলাম ‘আম্মা ঘোলা’। ক’দিন পরে কারা যেন জানালো ঘোড়ার গাড়ির পরিচয়। ঢাকার প্রধান বাহন ছিল এই ঘোড়ার গাড়ি, তখন। টুং টাং শব্দ করে চলতো রিক্সা, আঙ্গুলে গোনা যায় এমন। হঠাৎ হঠাৎ ঘোঁ ঘোঁ শব্দ করে যাচ্ছে বাস-গাড়ি একটি কি দু’টি। এই দৌড়াদৌড়ি দেখি আব্বার হাত ধরে। এ পর্যন্ত এসেই পথ হারিয়ে ফেলি। ঝিমধরা মগজ। নজরে ধূঁয়ার উড়াল। আবছা আবছা, ঠিক ঠাহর করা যায় না।
দু’তলা বাসায় পৌঁছে গেলাম একসময়। কখন কি করে পৌঁছলাম রিক্সায় না ঘোড়ার গাড়িতে এর কিছুই নজরে ভাসছে না। শুধু এটুকুই মনে আছে একতলা বাদ দিয়ে দু’তলা দালানে থাকা শুরু। দালানের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় ঘরে। সিঁড়ির সাথে প্রথম পরিচয় হলো। দেখা হলো, ভাব হলো। বারবার উঠানামা করি। উঠানামায় যেন একটা আলাদা আনন্দ।
যদিও আম্মার বারণ ছিলো সিঁড়িতে একা একা যাবে না। কে শোনে কার কথা। আম্মা আড়াল হলেই সিঁড়িটা বন্ধু হয়ে যেতো। একদিন ঘটলো বিপদ। পা ফসকে পড়ে গেলাম। গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে নিচে। মাথা, হাত, পা ফেটে ফোটে একাকার। আমি তখন ভয়ের ঘরে ঢুকে পড়েছি। কান্নার আওয়াজে ছুটে এলেন চাচা। তিনি থাকতেন নিচতলায়। সিঁড়ির লাগোয়া ঘরটিতে। এলেন চাচিও। আশেপাশের ঘর থেকে আরো দু-একজন বোধহয়। একটা বিতিকিচ্ছি অবস্থা। হইচই শুনে ছুটে এলেন আম্মা। রান্নাঘর বা কোথাও ছিলেন হয়তো। আমি তখন চাচার কোলে কাঁদছি, কাঁপছিও।। ভয়ে ব্যথায়। হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠলেন আম্মা। চাচি সামলালেন তাকে। এরি মধ্যে পাড়ার অষুধের দোকানে গেলেন দ্রæত চাচা। আমি তার কোলে। তখন তো আর সড়কের মোড়ে মোড়ে ক্লিনিক ছিলো না। অষুধের দোকান-কম্পাউন্ডাররাই ছিলো ভরসা। সেদিন লাটে উঠলো চাচার অফিস। আম্মার চোখ দুটি রক্তজবা। বসে আছে কান্নার আলামত। নতুন বাড়িতে উঠার দু’একদিনেই এমন দুর্ঘটনা। আম্মা অপয়া ভাবতে লাগলেন পরিবেশকে, দালানকে। হাতে ব্যান্ডেজ, কপালেও পট্টি। আম্মার বারণ না শুনলে বোধহয় এমনটাই ঘটে। বারকয়েক ঘুরপাক খেলো মগজে। এজাতিয় ভাবনা। আম্মাকে বকাঝকা করছিলেন আব্বা, ঘরে ফিরে। অপরাধ তো আমার, আম্মাকে কেনো বকাঝকা। সে কথা কি করে বোঝাই। সিঁড়িমুখো হইনে বেশ কদিন, এঘটনার পর থেকে। জানালার পাশে বসে বসেই সময় কাটে। এরি মধ্যে পাহারা বসিয়েছেন আম্মা। দরজায় ঝুলিয়ে দিলেন নিষেধের শিকল।
আব্বা এ বাসায় উঠেছিলেন চাচার পরামর্শে। দুইভাই পাশাপাশি থাকবেন। বিপদে-আপদে কাজে লাগবে এই ভরসায়। চাচার নাম আউলাদ হোসেন খান, আব্বার চাচাতো ভাই। কাজ করতেন কৃষি বিভাগ না সিভিল সার্ভিস যেনো। আর আব্বা ডাকবিভাগে। দুজনেই বের হন সকালে, ফিরে আসেন দুপুর যখন কিছুটা ঝুলে পড়ে। এভাবেই যাচ্ছে সূর্য প্রতিদিন, হেঁটে হেঁটে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। একদিন আব্বা একখানা বই নিয়ে এলেন, রঙিন পাতায় পাতায় ছবি ভরা। জীবনের প্রথম বই দেখা। হরফের সাথে দোস্তি। তখনো জানি না কোনটা কোন হরফ। এ বই পেয়ে আনন্দের আকাশে উড়তে থাকলাম। হরফ, ছড়া এবং ছবির সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেন সকাল-বিকাল, আম্মা। খুশির প্রজাপতি দাপাদাপি করে মনে, চোখের তারায়। অ আ ক খ শিখতে চেষ্টা করি, মুখস্থ করি আর ছবিগুলো দেখি বারবার। বই ঘেটে ঘেটে সময় কাটে। পড়ে পড়ে শোনান আম্মা। প্রতিটি হরফের পাশে ছবি, সাথে কয়েক লাইনের ছড়া-কবিতা। এক মজার খেলায় মেতে উঠলাম। এভাবে বেশ কটি ছড়া শিখে ফেললাম, গোটাকয়েক হরফও। নতুন কোনো বাগানে ঢুকে পড়েছি মনে হলো। সে বাগানে নাম না জানা কতো ফুল, নানা রঙের নানা গন্ধের। ঘুরে ফিরে দেখি বাগান সকাল-বিকাল। তাতে আব্বার চোখের তারায় উড়ে খুশির পাপড়ি। আনন্দের নূপুর বাজে আম্মার মনে। ছড়া-ছবি, হরফ, কাকে রেখে কাকে পড়ি, দেখি। পাখির ছবি, মাছের ছবি, মানুষের ছবি নৌকার ছবি। হাতির ছবি দেখে তো অবাক। এটি আবার কি জিনিস, কেমন জন্তু। আম্মা জানালেন এর নাম হাতি। খুব শক্তিশালী এ প্রাণীটি। শুঁড় দিয়ে নাকি বড় বড় গাছ উপড়ে ফেলে। তখনি এই প্রাণিটির প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। দেখার ইচ্ছা জাগে। কোথায় হাতির ঘর-বাড়ি? এমন ভাবনা উঁকি দিতেই ভয় এসে ভিড় করে মনে। শক্তিমানদের কেনা ভয় পায়। বয়স ছোট, মনও ছোট, তাই বইয়ের ছবির মধ্যেই আটকে রাখলাম ইচ্ছা-ভাবনা, দেখা।

তিন.
এরই মধ্যে হাঁটতে থাকলো বেশ কিছু ছড়া-ছবি মনের বারান্দায়। অন্যরকম আনন্দের ফুরফুরে বাতাস, একবার পুবে আরেকবার পশ্চিমে উড়ে যায়। ওরা যেনো একেকটি মাছরাঙা। মনের দীঘিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হঠাৎ হঠাৎ। আম্মা পাঠক, আমি শ্রোতা। প্রায় প্রতিদিনই আসর বসে পাঠের। মাঝে-মধ্যে যোগ দেন আব্বাও আমাদের পাঠআসরে। পাখির পিঠে চড়ে যেনো চলে যাচ্ছে সময়। ইতিমধ্যে ভাঁজ পড়ে গেছে অনেকগুলো, বইয়ের পাতায়, মলাটে। পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতেই একদিন আবিষ্কার করলাম ঝাকড়া চুলওয়ালা একটি ছবি। বড় বড় চোখ। অন্যরকম, অন্য কায়দার। আর মানুষজনদের থেকে আলাদা, চেহারা-সুরতে। ছবির নিচে দু লাইনের একটি ছড়া। এখানে এসেই চোখ দাঁড়িয়ে থাকে। বারবার দেখতে ইচ্ছা করে ছবির মানুষটি। আম্মা বুঝতে পারলেন মনের ভাবনা। তাই ছবির মানুষটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। জানালেন ছবিতে যাকে দেখা যাচ্ছে তাঁর নাম কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি মস্তবড় কবি। এরপর নিচের ছড়াটি পাঠ করে শোনালেন ‘বাংলার বুলবুল মহাকবি নজরুল’। কবি, কবিতা, মহাকবি এসব শব্দের সাথে এই প্রথমবারের মতো পরিচয়। কবিতার মহাকবি নজরুল চোখের তারায় গিয়ে ঘর বাঁধলেন প্রথম পরিচয়ে। এখনো তিনি সে ঘরেই বসবাস করছেন। হয়তো এজন্যই কবিতা বন্ধু হয়ে গেলো একসময়। বন্ধু হয়ে থাকলো কবি নজরুলও। ঝাকড়া চুলওয়ালা বড় বড় চোখের ছবির মানুষটি।
একতলা বাসায় যখন ছিলাম তখনো ওদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হতো, সকাল-সন্ধ্যা। দোতলায় এসেও দেখি ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে। কখনো একা আবার কখনো দল বেঁধে। প্রথম প্রথম ভয়ে কুঁকড়ে আসতো শরীর মন। পরে অবশ্য ভয়েরা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনো হাঁটে পাশাপাশি। দালানের কার্নিশে বসে থাকে ওরা। একজন আরেকজনের পিঠ চুলকায়। কি যেনো খুঁজে খুঁজে তুলে আনে। তারপর মুখে পুরে দেয় আঙ্গুল। এমন দৃশ্য রোজ দেখি, জানালায় বসে বসে। ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আব্বা কদিন আগে। এদের নাম বানর। বাঁদরামি করা ওদের স্বভাব। তাই ভুলেও কাছে ঘেঁষবে না। আম্মাকেও সাবধান করে দিয়েছিলেন। বানরের বাঁদরামি দেখে দেখে সময় কাটে আমার। প্রতিটি ছাদ দাপিয়ে বেড়ায়। মাঝে-মধ্যে উধাও হয়ে যেতো ওরা। কই যায় কার কাছে যায়? আব্বা আম্মার কাছে যায়? নানুবাড়ি না দাদুবাড়ি? এরকম নানান জিজ্ঞাসা মনের চারপাশে ভিড় করতো।
আকাশের মাঝ বরাবর উঠে আসতো সূর্য এক সময়। তখন দুপুর নামতো এলাকায় চুপচাপ। ঝুরঝুর ঝরতো রোদের কিরণ বাড়িগুলোর ছাদে, উঠানে। ঝিমধরা পাতার ফাঁকফোকরে শালিকের ঝাঁক। একটি দুটি কাক গাছের ডালে, বিদ্যুতের তারে ঝুলতো। বাতাসে রোদের ঝাঁজ, ধোঁয়া ধোঁয়া রঙ। দূরে ভাঙাবাড়ি দাঁড়িয়ে আছে একা। একটি কুকুর শুয়ে থাকতো সেখানে।
চোখাচোখি হতো তার সাথে রোজ। কাছে গিয়ে বসতে মন চাইতো। কিন্তু যাওয়া হয়নি কোনো দিন। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে অপেক্ষা করতো বানরের দল ছায়ামতো জায়গা দেখে। দুপুর থিথিয়ে এলে আবার সেই বাদরামী। ছাদ থেকে ছাদে লাফালাফি। বলতে গলে পাড়াটি ছেলো বানরময়। সন্ধ্যার আগে আগে মনে হতো বানর আর মানুষ সমান সমান এ পাড়ায়। যে জন্যে যন্ত্রনার শেষ ছিল না। একটু অসাবধান হলেই বিপদ লাফিয়ে আসত। ঘরের খাবার চুরি তো প্রতিদিনের যন্ত্রণা। আসবাবপত্র কাপড় চোপর তচনচ করতো। বাচ্চাদের ভয় দেখাতো। বড়রাও বানরদের বিরক্ত করতো না, ভয় তাদেরকেও তারিয়ে ফিরতো। এত ঝুটঝামেলার পরও বানরের পাশাপাশিই ছিল আমাদের বসবাস। এভাবেই কাটতো দুপুরের কতকটা সময়।
একসময় বিকাল নামতো পাড়াজুড়ে। একজন দু’জন করে নেমে আসত রাস্তায়। কেউ কেউ জড়ো হতো খোলা মতো জায়গায়। জমে উঠতো নানা ধরনের খেলা। মাগরিবের আজানের আগ পর্যন্ত। আজানের আওয়াজ কানে বাজতেই খেলার ডানা গুটিয়ে আনতো সবাই। পাখিরাও ফিরতো যার যার নিড়ে। নিরবতা ঝরতো আধো আলো আধো আঁধারে। কোনো কোনো বাড়িতে বাজতো ঘন্টা, পূঁজার ঘন্টা। ছুটাছুটি করতো ফুলের গন্ধ। জোনাকির ওড়াওড়ি ঝোপঝারের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে। তখন ঘরে ঘরে চলতো হারিকেন জ্বালানোর আয়োজন। প্রায় প্রতিদিন দেখতাম হারিকেন পরিষ্কার করছেন আম্মা। মোহাম্মদ আলী ভাই বাসায় থাকলে এ কাজটি তার ভাগেই পড়তো। কেরোসিনের গন্ধটা বেশ ফুরফুরে। তাই কাছে পিছেই বসে থাকতাম রোজ। সলতায় আগুন ছোঁয়াতেই জ্বলে উঠতো হারিকেন। আঙ্গুন জ্বালার দৃশ্যটা ভয়ের কাঁপন তুলতো মনে। আবার দোল খেতো আনন্দের ঝালর। কারণ ঢাকা পড়তো অন্ধকার; দৌড়ে আসতো আলো। তখনতো আর বিজলী বাতি ছিল না ঘরে ঘরে। হারিকেনই ছিল ভরসা। বলতে গেলে নব্বই জনের বাড়িতে। যদিও রাস্তার ধারে জ্বলতো বিজলী বাতি, মিটমিট।
জীবনঘুড়ির আকাশ দেখা খ্যাতিমান শিশুসাহিত্যিক, কবি ও ছড়াকার সাজ্জাদ হোসাইন খানের জীবনের গল্প (ধারাবাহিক চলবে)





