সম্ভবত ১৯৭৬ সালে জামালপুর শহরে এক বৈকালিক আড্ডায় তার নাম প্রথম শুনি। যার মুখে শুনলাম কবিতার সঙ্গে তার কোনও রিসতাদারি নেই। কিন্তু সুখ্যাতি শুনেছেন। সেই থেকেই নামটি মনে গেঁথে আছে। তখনও জানি না দুবছর পর ঢাকায় পড়তে এসে আমি সবার আগে কিনবো কাব্যগ্রন্থ ‘সোনালী কাবিন’। তখনও জানি না, আরও বছর ছয়েক পর ১৯৮৫-৮৬ সালে শব্দের তুলিতে স্বপ্নের রঙ ছিটানো এক শিল্পীর সঙ্গে দেখা হবে শিল্পকলায় তার কর্মস্থলের ছোট্ট কক্ষে। হ্যাঁ, তিনি কবি আল মাহমুদ। বাংলা ভাষা যার হাতের পেলব স্পর্শে, আদরে বিগলিত কৃতার্থ।
এখনও চোখ বুজে দেখে নিতে পারি, নিজের অফিস কক্ষে বসে আছেন কবি আল মাহমুদ। কথা বলছেন স্বভাবসম্মত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে। বলছেন কবিতার কথা, কবিদের কথা, নিজের কথা। কবিতার কথা বলতে গিয়ে অনর্গল উদ্ধৃতি দিচ্ছেন সেইসব অজানা অচেনা কবিদের কবিতা থেকে, যারা ইতিহাসের প্রায়ান্ধকার গলিপথে হেঁটে চলে গেছেন। বলছেন আবদুল হাকিম, শাহ মোহাম্মদ সগীর বা আলাওলের কবিতা থেকে। সাহিত্যের শিক্ষার্থী হিসাবে এসব পূর্বগামীদের নাম জানা ছিল। আবদুল হাকিমের ‘যেসবে বঙ্গেত জন্মি’ ইত্যাদি দুয়েকটি চরণও জানা।
কিন্তু তাদের কবিতা কারও ঠোঁটস্থ থাকবে কখনও ভাবনাতেও আসেনি। সেই আমার প্রথম কোনও সত্যিকারের কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ। আমি কতকটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যেই যেন জেগে উঠলাম। এর অনেক বছর পর তাঁকে সহকর্মী হিসাবেও পেয়েছি। তার একটির পর একটি বই প্রকাশ পেতে দেখেছি, পড়েছি। আর চমৎকৃত জিজ্ঞাসায় বিদ্ধ হয়েছি, মনের ভাবনাগুলো, সহজ সরল অনুভূতিগুলো মোহন শব্দ ও ছন্দের কাঠামোর ওপর বসিয়ে কী করে তিনি নীল নীল, ঘুম ঘুম স্বপ্ন বানিয়ে ফেলেন? আমি কখনও কবিকে এসব জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। বড় মানুষদের সামনে গেলে আমি কেমন যেন খোলসে আবৃত অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাই।
তবে কাজটি অর্থাৎ কবির কারিশমার রহস্য উদ্ঘাটন অনিষ্পন্ন থাকেনি। আমাদের অনুজপ্রতীম প্রাক্তন সহকর্মী, সিলেটের সাঈদ চৌধুরী দীর্ঘকাল ধরে গভীর মনোযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজটি করেছেন। তিনি কখনও ঢাকায়, কখনও সিলেটে, কখনও ঢাকা-সিলেট যাত্রাপথে রেলে বা গাড়িতে বসে বহুবার কবি আল মাহমুদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। বের করে এনেছেন একজন স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্ন দেখানো জাদুকরের স্বপ্নের সৃৃজন ও সঞ্চালনের রহস্যকথা। তুলে এনেছেন কোন রসায়নে তিনি পাঠকের মনের মধ্যে স্বপ্ন সঞ্চালন করেন, কীভাবে তৈরি করেন সেই স্বপ্নজাল। আর এইসব বৃত্তান্ত সাঈদ চৌধুরী তুলে ধরেছেন তার বইতে।
কবি আল মাহমুদের সাক্ষাৎকার নিয়ে সাঈদ চৌধুরীর বইটির নাম, ‘কালজয়ী কবিতার স্রষ্টা আল মাহমুদ’। এটি অত্যন্ত অভিনিবেশের সঙ্গে লেখা একটি বই যা দেশের এক প্রধান কবির জীবন ও কবিকৃতির ওপর ঘনিষ্ঠভাবে আলোকপাত করে। সাঈদ চৌধুরী কবির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘কবি আল মাহমুদ বাংলা কবিতাকে গৌরবোজ্জ্বল অবস্থানে নিয়ে এসেছেন। আমাদের কবিতায় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার যে উন্মেষ ঘটেছে তিনিই তার নায়ক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং আল মাহমুদ যেন এক ও অভিন্ন।’ এই মন্তব্য যথার্থ।
কবি প্রসঙ্গে তিনি বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদের উদ্ধৃতি তুলে ধরেন। লিখছেন, ‘প্রখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের মতে, সমকালীন যে দুজন বাঙালী কবির দুর্দান্ত মৌলিকতা এবং বহমানতা আমাকে বারবার আকৃষ্ট করেছে, তাদের একজন বাংলাদেশের আল মাহমুদ, অন্যজন পশ্চিমবঙ্গের শক্তি চট্টোপাধ্যায়।’
সিলেটের পাণ্ডুলিপি প্রকাশনের এই বই প্রকাশ পেয়েছে কবির মৃত্যুর আগে ২০১৮ সালের ১১ জুলাই কবির ৮৩তম জন্মদিনে। আল মাহমুদ ফাউন্ডেশন ও ফেসবুক ফ্যানপেজ প্রিয় আল মাহমুদের যৌথ আয়োজনে ওই অনুষ্ঠানে কবি নিজের হাতে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন।
বইটির সবচেয়ে ভালো দিক হলো, এই বইয়ের প্রায় পুরোটাই প্রকাশের আগে কবিকে দেখিয়ে নিয়েছিলেন লেখক। সুতরাং এতে কবির যা কিছু বক্তব্য উঠে এসেছে তার পুরোটাই কবির পূর্বানুমোদন পাওয়া।
লেখক সাঈদ চৌধুরী বলেন, ‘একজন প্রধান কবির চোখে দেখা জীবন ও জগতের অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করে। তার সাধনা ও ভাবনাগুলো একত্রিত করতে পারলে আগামীতে লেখক-গবেষকদের কাজ সহজ হবে। এই প্রত্যাশা থেকে তিন যুগ ধরে কাছে থেকে দেখা আল মাহমুদকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রয়াসে এটি এক ভিন্ন রকম আলাপচারিতা।’
নানা ধরণের প্রশ্ন ঠেলে দিয়ে কবি আল মাহমুদের জন্ম, বংশ পরিচয়, তার শিক্ষাদীক্ষা, পারিবারিক-সামাজিক পরিবেশ, কবিতার হাতেখড়ি থেকে শুরু করে রাজনীতি, আদর্শ, বিচ্যুতি, বিতর্ক, বন্ধু কবিদের সঙ্গে কাব্যিক ঈর্ষা, কর্ম-জীবন, সাফল্যের পেছনের সম্ভাব্য কারণ, জীবন-দর্শন ইত্যাদি সব কিছুই উঠিয়ে এনেছেন সাঈদ চৌধুরী।
প্রায় কোনও কিছুই বাদ পড়েনি। একজন কবির প্রতি এক গবেষকের এই গভীর অনুসন্ধিৎসা ও একনিষ্ঠভাবে লেগে থাকা এটি কবির ভক্তদের জন্য বিরাট পাওয়া। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কাজের প্রতি, এক্ষেত্রে কবিতা ও কবির প্রতি, এরকম নিবেদিতপ্রাণ মানুষ ছাড়া কোনও জাতিই তার প্রকৃত বীরদের কথা জানতে পারে না। সেদিক থেকে বাঙালি মুসলমান দুর্ভাগা। গত দেড় দুশো বছরে এই বাংলাদেশ ভূ-খণ্ড এমন অসংখ্য কৃতি সন্তানের জন্ম দিয়েছে যাদের জীবনী তো দূরের কথা, তাদের সব কৃতিত্বও আমরা ভুলে গেছি অথবা হারিয়ে ফেলেছি। সাঈদ চৌধুরীর কাজ এই কারণেই বিশিষ্ট ও ব্যতিক্রমী।
আমরা সাঈদ চৌধুরী ও কবি আল মাহমুদের আলাপচারিতায় উঠে আসা কবির জীবন এক নজরে দেখে নিতে পারি। সাঈদ লিখছেন, জানতে চাইলাম, সারা জীবন কবিতার সাথে ঘর-সংসার করলেন। এখন এ নিয়ে ভাবতে কেমন লাগে? আল মাহমুদ বললেন, ‘জীবনের পড়ন্ত বেলায় কবিতা নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে। অতীতকে স্মরণ করে আমি ভীষণ আনন্দ বোধ করি। একসময় কবিতাই ছিল আমার একমাত্র আরাধনার বিষয়।’
প্রশ্ন: আপনার পিতৃপুরুষের গল্প শুনেছি। ধর্মপ্রচারক হিসেবে এদেশে তাদের আগমন। আপনার জীবনে তাদের প্রভাব কতটুকু?
আল মাহমুদ: আমি আমার নয় পুরুষের নাম জানি। এরা বাইরে থেকে এসেছিলেন। ধর্ম প্রচারক ছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌড়াইল মোল্লাবাড়ি হল আমার জন্মস্থান। এই বাড়িতেই ১১ জুলাই ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আমার জন্ম। আমার ডাকনাম ছিল পিয়ারু। সে-সময় কলকাতায় পিয়ারু নামে বিখ্যাত এক কাওয়ালি গায়ক ছিলেন। আমার আব্বা ছিলেন তার গানের ভক্ত। ওই কাওয়ালি গায়কের নামে তিনি আমাকে পিয়ারু বলে ডাকতেন। অনেক আদর করে রেখেছিলেন নামটি। প্রথম যে স্কুলে লেখাপড়া করেছি, আমাদের বাড়ি থেকে সেটা ছিল অনেক দূরে- নাম মিডল ইংলিশ স্কুল। প্রথম দিন স্কুলে একটা আচকান পরে গিয়েছিলাম। ক্লাসে ঢুকেই দেখি, আমার সহপাঠী সবাই ব্রাহ্মণের ছেলে, উঁচুজাত। একদম শেষ বেঞ্চে একটা মুসলমান ছেলে ছিল- তার নাম রহমতুল্লাহ। একেবারে নিরীহ গোছের গরীব মানুষ। আমি ব্রাহ্মণ সহপাঠীদের পাশে বসলাম। বিষয়টি তারা সহজভাবে নেয়নি। এমনকি শিক্ষক মশাইও ভাল চোখে দেখেননি। সেদিন যে শিক্ষক আমাদের ক্লাস নিলেন, তার নাম গজেন্দ্র বিশ্বাস। তিনি আমাকে বললেন, তুমিই মোল্লা বাড়ির ছেলে? আমি মাথা নাড়ালাম। স্যার তখন হাসতে হাসতে বললেন, এতদিন বামুন-কয়েতদের পিটিয়ে মানুষ করেছি, এখন মোল্লা এসে হাজির হয়েছে।
নিজের পরিবারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রসঙ্গে বলছেন আল মাহমুদ। ‘আমার দাদা-দাদি নিজেদের মধ্যে চোস্ত ফার্সিতে কথা বলছেন, ছেলেবেলায় এটা আমি নিজেই দেখেছি। আমার পরিবারের লোকজন কবিতা পড়তেন- উর্দু ও ফার্সি ক্লাসিকাল কবিতা। দাদির মুখেই প্রথম শুনেছি শাহনামা’র কাহিনি। আমার দাদা মীর আবদুল ওয়াহাব কবি ছিলেন। জারি-সারি লিখতেন।’ বলেছেন, ‘পারিবারিক সাহিত্য চর্চার একটা প্রভাব আমার মধ্যে জন্মেছিল। প্রথম যখন লেখালেখি শুরু করি, তখন আমি অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। আজ মনে হয়, দাদা কবিতা লিখতেন বলে পরিবারে আমার লেখালেখিও সাদরে গৃহীত হয়েছিল।’
কবিতা আপনার রক্তের মধ্যে ছিল নাকি সাধনার মাধ্যমে অর্জিত? এমন এক প্রশ্নে কবি যা বলছেন সেটি এক চিরসত্যের আভাস দেয়। বলছেন, ‘কবিতা অনেক সাধনা আর পরিশ্রমের কাজ। এজন্য অনেক কসরত করতে হয়েছে। কবিতার ছন্দ, অন্তমিল ইত্যাদি নিয়ে ভেবেছি, প্রচুর পড়াশোনা করেছি। যদিও লেখার কাজটা সবার কাজ নয়, তা যদি হতো তাহলে তো কেরানিরাই জগতের শ্রেষ্ঠ লেখক হতেন। আমি যে কবি, এটা সম্ভবত আমার রক্তের মধ্যে ছিল।’ প্রসঙ্গত আরও বলছেন, ‘যে দেশে কবি জন্মায় না সেখানে প্রকৃতিও আক্ষেপের ধ্বনি তুলতে থাকে। সৌভাগ্য সেই দেশের, যে মাটিতে একজন ভাল কবির জন্ম হয়েছে।’
নর-নারীর প্রেম প্রসঙ্গ: যে কবি উচ্চারণ করেন সেই অবিস্মরণীয় পংক্তি: ‘জ্ঞানে ও অজ্ঞানে দ্রোঁহে পরস্পর হবো চিরচেনা / পরাজিত নই নারী, পরাজিত হয় না কবিরা / দারুণ আহত বটে আর্ত আজ শিরা-উপশিরা।’
সেই কবির গার্হস্থ্য প্রেমের অনুভব, ‘নর-নারী একে অন্যকে বিশ্বাস করে ঘর বাঁধে, এই বিশ্বাসটুকু না থাকলে জগৎ অরণ্যে পর্যবসিত হতো। আর এই বিশ্বাসের নামই হলো প্রেম। একে অন্যের জন্য পাগল হওয়ার নাম প্রেম নয়। প্রেম হলো এক স্বর্গীয় অনুভূতি। এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে জগতের শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল কর্ম। সব শিল্পীই এই জায়গায় একবার নীরবে দাঁড়ায়। মানবিকতা, প্রেম একই সাথে প্রেমের পরিণতির প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।’
কবিতা লেখার অপরাধে পুলিশি ধাওয়া খেয়ে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হওয়া আল মাহমুদের নিয়তির মত। সেই ঘটনা সবিস্তারে এসেছে সাঈদ চৌধুরীর বইতে। আল মাহমুদ বলেন, ‘৫২-র ভাষা আন্দোলনের ঢেউ তখন মফস্বল শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আছড়ে পড়ছে। স্থানীয় ভাষা আন্দোলন কমিটির লিফলেটে আমার চার লাইন কবিতা ছাপা হয়েছিল। লিফলেটগুলো তখনো বিলি হয়নি। এরই মাঝে আমাদের বাড়িতে পুলিশ হানা দেয়। পরে জেনেছিলাম প্রেস থেকে লিফলেটের কপি ডিআইবির লোকদের হস্তগত হলে তারা আমার নামসহ কবিতা দেখতে পায়। এতে অন্য কারো নামধাম ছিল না- ছিল শুধু ভাষা আন্দোলন কমিটি। ফলে এই আন্দোলনে কারা কারা জড়িত আছে সে তথ্য বের করার জন্য আমাদের বাড়িতে হানা দেয়।’
ওই ঘটনার পর আল মাহমুদ আত্মগোপনে চলে যান। আর কখনই তার স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য পৈত্রিক বাড়িতে যাওয়া হয়নি। বলেছেন, ‘ওই ঘটনা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কবিতার জন্য অমি ঘরছাড়া হই। আমি আমার কবিতার শক্তি অনুভব করতে থাকি।’
‘…চট্টগ্রামে থাকাবস্থায় প্রতিবেশী ছিলেন গায়ক শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব। কবিতা লিখি বলে তিনি খুব খাতির করতেন আমাকে- একেবারে আগলে রাখতেন। আমাদের পাশেই থাকতেন অনেক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নারী। আমাকে তারা কবি বলে ডাকতেন। তাদের সাথে এক ধরণের সখ্য গড়ে ওঠে। তাদের নিয়েই লেখা হয় আমার সবচেয়ে আলোচিত সনেটগুলো। চৌদ্দটা সনেটের মধ্যে প্রথম সাতটা একটানা লিখেছি। লেখার পর নিজেরই মনে হয়েছিল, অন্যরকম কিছু একটা লিখেছি। সবগুলোই বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হলো। আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠল।’
প্রশ্ন: কোন কাগজে কবিতা ছাপার পর নিজেকে বেশি প্রফুল্ল মনে হয়েছে?
আল মাহমুদ: বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকায়। এখনো মনে আছে, বুদ্ধদেবকে একসঙ্গে তিনটি কবিতা পাঠিয়েছিলাম। ক’দিন পর বুদ্ধদেব বসু’র চিঠি পেলাম। পোস্টকার্ডে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন, প্রীতিভাজনেষু, তোমার একটি বা দু’টি কবিতা ছাপা যাবে বলে মনে হচ্ছে। সেই পোস্টকার্ডটি অনেকদিন পর্যন্ত আমি সংরক্ষণ করেছি। বাংলা ভাষার একজন নবীন কবির জন্য এটি ছিল অসাধারণ প্রেরণা ও স্বীকৃতির বিষয়।
লেখালেখিতে দায়বদ্ধতার প্রশ্নে কবির দর্শন উল্লেখযোগ্য, ‘দায়বদ্ধতা এক অদৃশ্য বিবেক। আমি বিবেকের তাড়নায় লিখি। আমাদের সমকালীন সাহিত্যে নানা বিষয়ে আমাকে সজাগ থাকতে হয়।’
অন্য এক প্রশ্নের জবাবে বলছেন, ‘লেখার বিষয় কী হবে, তা আগে থেকে স্থির করে নিতে পারি না। আমি লিখি কোনো তাৎক্ষণিক উদ্দীপনায় কিংবা অন্তরের তাগিদে। যেহেতু আমি কবি ছাড়া আর কিছু নই, সে কারণে বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যেতে চেয়েছি। কেমন হয় কবিরা? কোথায়, কীভাবে জন্মায় একজন কবি? কবির কী প্রয়োজন একটি দেশের জন্য? এসব প্রশ্নের জবাব অতীতে দেয়ার চেষ্টা করেছি। অনেক কথা লিখেছি, যা অন্য কবিরা লিখতে সম্মত হবেন না। আমি লিখেছি; কারণ আমি আমার পাঠকদের কাছে সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই।’ তার উপন্যাসের উপাদান প্রসঙ্গে বলছেন, ‘আমি মনে করি, উপন্যাস রচয়িতাদের নিজের জীবন ছাড়া লেখার আর কোনো বিষয়বস্তু থাকে না। থাকলেও সেটা শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনেই এসে মিশে যায়। আমিও এর ব্যতিক্রম নই।’
কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে: ‘একটা দেশের সাথে একজন কবির রক্ত-মাংস জড়িত। দেশ যেমন থাকে একজন কবিও তেমনি থাকেন, তার অন্য কোনো ভালো-মন্দ নেই। আমি কবি। আমি স্বপ্নের কথা বললেও স্বপ্ন আমার খাদ্য নয়। আমি স্বপ্ন ভাঙিয়ে খুচরো পয়সার মতো নানা দুঃখ, অশ্রুজল ও অনুভূতি ক্রয় করে থাকি। যদিও লেখাটাই আমার পেশা। অন্য জীবিকায় যেতে মন চায়নি। আমার জাতির জন্য আমার যা করণীয় ছিল, তা করেছি, কোনো পুরস্কার বা তিরস্কারের কথা ভেবে নয়।’
প্রথম কবিতা লেখার অনুভূতি: ‘প্রথমত কবিতা পড়তে ভালো লাগত- কেমন যেন ঘোরের মতো। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে ত্রিশের দশকের সব কবির বই-ই পড়েছি। মনে আছে, জীবনানন্দ দাশের ‘ধূসর পান্ডুলিপি’ পড়ে মনের মধ্যে কেমন যেন হলো। মনে হলো, এ এক অন্য রকম জিনিস! এভাবে পড়তে পড়তেই আগ্রহ জেগে উঠল- কী খেয়ালে লিখে ফেললাম কবিতা। তখন মনে হয়েছিল, আমিও তো পারি! তখন পত্র-পত্রিকায় অনেক সংকোচ নিয়ে লেখা পাঠাতাম। সেটা ছাপা হয়ে যেত। সুখের কথা হলো, আমার কোনো লেখাই পত্রিকার সম্পাদকদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়নি।’
স্বাধীনতা যুদ্ধে সম্পৃক্ততা: ‘স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কোলকাতায় চলে গেলাম। আমার ভগ্নিপতি তৌফিক ইমামের সহায়তায় অস্থায়ী রাষ্টপতি তাজ উদ্দিন আহমদ আমাকে একটি কাজ দিলেন। প্রবাসী সরকারের স্টাফ অফিসার পদে। ৮নং থিয়েটার রোডে ছিলাম। দেশে চলমান যুদ্ধের খরব নেয়া ও লেখালেখি। আমাদের বীর জনগণ সর্বশক্তি নিয়ে আক্রমণকারী পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, সেই খবর ছড়িয়ে দেয়া ছিল আমাদের কাজ।’
জিতে যাওয়ার গল্প: আলাপচারিতায় সব সময়ই অকপট ছিলেন আল মাহমুদ। অনেক সময় নিতান্ত সরলও। পাঠকের স্বতস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত কবি বলেন, ‘কখনও আকস্মিকভাবে আমার ঘরে টেলিফোন বেজে ওঠে। তারা আমার পাঠক। কী বার্তা, যখন জিজ্ঞেস করি তখন উত্তর আসে, আপনি লিখে যান, শুধু লিখে যান। এ কথায় আমার অন্তরাত্মায় আনন্দের ফোয়ারা উদ্ভাসিত হতে থাকে। ভাবি আমার লেখা পৌঁছে গেছে। আমি যেখানে যেতে পারিনি কোনো দিন, যেখানে ছিলাম না সেখানেও আমার আত্মার শক্তি আত্মীয়তা বৃদ্ধি করে চলেছে। এর চেয়ে বড় সার্থকতা কবির জন্য আর কী হতে পারে?’
আরও বলছেন, ‘আমার মা জানতেন, তার একটি ছেলে কবি হৃদয় নিয়ে জন্মেছে। আর সব ছেলের মতো নয় সে। বিষয়বুদ্ধিহীন এই বালকটির জন্য আমার মায়ের দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। তিনি জানতেন, একে সবাই ঠকাবে। আর আমি জানতাম, সবার কাছে ঠকেও কিভাবে জিতে যাবো।’
আল মাহমুদ জিতে গেছেন। বিজয়ী কবি হিসাবে দেশের মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে তিনি চিরবিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তার লেখা টিকে আছে, থাকবে আরও বহু বহু দিন, হয়তো পৃথিবীতে যতদিন বাংলা ভাষা টিকে থাকবে ততদিনই। কারণ, সত্যিকারের কবির কখনও মৃত্যু হয় না। তারা অমর।
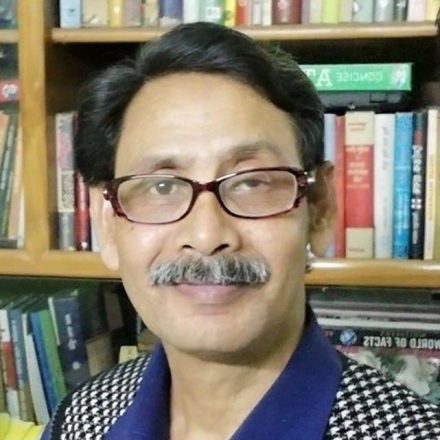 * মুজতাহিদ ফারুকী কবি ও কলামিস্ট, সহকারী সম্পাদক দৈনিক নয়াদিগন্ত
* মুজতাহিদ ফারুকী কবি ও কলামিস্ট, সহকারী সম্পাদক দৈনিক নয়াদিগন্ত





